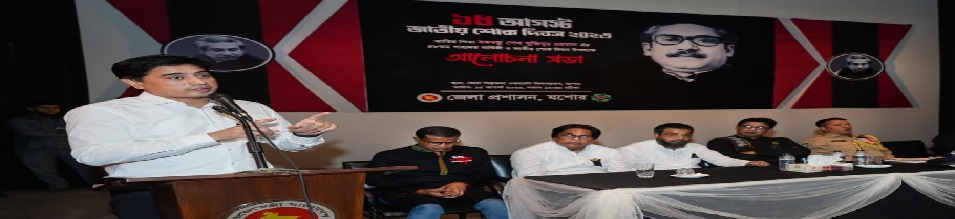-
-
প্রথম পাতা
-
-
জেলা সম্পর্কিত
ঐশ্বর্য ঐতিহ্যের যশোর (যশোরের প্রশাসনিক ইতিহাস)
-
স্বাধীন রাজা প্রতাপাদিত্য
-
যশোরের রাজাদের ইতিহাস, বিশেষত চাঁচড়া রাজার পারিবারিক ইতিহাস,
-
বিখ্যাত জমিদারগণ ও জমিদারি প্রশাসন
-
জেলার ভূ-সম্পত্তির বিভাজন এবং নতুন জমিদারের ইতিহাস
-
১৭৮১ সালে যশোর জেলায় বৃটিশ প্রশাসনের প্রতিষ্ঠা
-
প্রথম ম্যাজিস্ট্রেট ও জাজ জনাব টিলম্যান হেঙ্কেল এবং তার সহকারী জনাব রকি
-
১৭৮৬ সালে যশোর কালেক্টরেট প্রতিষ্ঠার ইতিহাস
-
যশোর কালেক্টরের দায়িত্ব ও কর্তব্য
-
ভূমি রাজস্ব প্রশাসনের ইতিহাস
-
অন্যান্য খাতভিত্তিক রাজস্ব প্রশাসন
-
প্রাথমিক পুলিশ প্রশাসন (১৭৮১-৯০) ও অপরাধচিত্র
-
অপরাধ বিচারিক প্রশাসন (১৭৮১-৯০)
-
দেওয়ানী বিচার প্রশাসন (১৭৮১-৯০)
-
দেওয়ানী মামলার বিচারকের ক্ষমতা বৃদ্ধি
-
স্বাধীন রাজা প্রতাপাদিত্য
- জেলা প্রশাসন
-
সরকারি অফিস
শিক্ষা ও সংস্কৃতি
-
জেলা শিক্ষা অফিস, যশোর
-
জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস
-
জেলা শিল্পকলা একাডেমী
-
বাংলাদেশ শিশু একাডেমী
-
যশোর পিটিআই,যশোর
-
জেলা উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো, যশোর
-
যশোর পলিটেকনিক ইন্সটিটিঊট,যশোর
-
সরকারি টিচার্স ট্রেনিং কলেজ
-
জেলা সরকারি গণগ্রন্থাগার, যশোর
-
কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, যশোর
-
টেক্সটাইল ভোকেশনাল ইন্সটিটিউট, যশোর।
মানব সম্পদ উন্নয়ন বিষয়ক
-
বিসিক জেলা কার্যালয়, যশোর
-
জেলা সমাজসেবা কার্যালয়
-
শহর সমাজসেবা কার্যালয়, যশোর
-
হাসপাতাল সমাজসেবা কার্যালয়, যশোর
-
প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্র, যশোর
-
প্রবেশন অফিসারের কার্যালয়, যশোর
-
সরকারি শিশু পরিবার বালিকা, যশোর
-
যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, যশোর
-
মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর,যশোর।
-
বিআরডিবি
-
জেলা সমবায় কর্মকর্তার কার্যালয়, যশোর।
-
জেলা কর্মসংস্থান ও জনশক্তি অফিস,যশোর
-
ইসলামিক ফাউন্ডেশন
-
জেলা ক্রীড়া অফিসারের কার্যালয়,যশোর
-
জাতীয় মহিলা সংস্থা, জেলা অফিস, যশোর
কৃষি, মৎস্য, প্রাণি ও খাদ্য বিষয়ক
-
কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, যশোর
-
জেলা মৎস্য অফিসারের কার্যালয়, যশোর
-
বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (সার) যশোর অঞ্চল , যশোর
-
জেলা প্রাণিসম্পদ অফিস
-
জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়, যশোর
-
আঞ্চলিক কৃষি গবেষণা কেন্দ্র, যশোর
-
জেলা কৃত্রিম প্রজনন কেন্দ্র, যশোর
-
সরকারী হাঁস মুরগি খামার, যশোর
-
আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কর্মকর্তার কার্যালয়, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, যশোর।
-
বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বীজ), যশোর
-
তুলা উন্নয়ন বোর্ড,যশোর
-
কৃষি বিপণন অধিদপ্তর
-
পাট অধিদপ্তর,যশোর
-
জেলা বীজ প্রত্যয়ন অফিসারের কার্যালয়,যশোর
-
মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইন্সটিটিউট(এস আর ডি আই), যশোর
-
তত্ত্ববধায়ক প্রকৌশলী কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন
-
বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ, যশোর
-
মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট, আঞ্চলিক গবেষণাগার, যশোর
-
আঞ্চলিক প্রাণিরোগ অনুসন্ধান গবেষণাগার (এফডিআইএল), যশোর
প্রকৌশল এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি
-
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর, যশোর
-
কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর, যশোর
-
নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয়, স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর(এইচইডি), যশোর বিভাগ
-
জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন
-
নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয়, স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর(এইচইডি), যশোর বিভাগ
-
জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর
-
গণপূর্ত বিভাগ
-
নির্বাহী প্রকৌশলী (সওকা), বিএডিসি, যশোর রিজিয়ন, যশোর
-
স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর
-
সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর , যশোর
-
পানি উন্নয়ন বোর্ড
-
বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ-২, ওজোপাডিকো, যশোর
-
বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ-১, ওজোপাডিকো, যশোর
-
যশোর পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-১
-
যশোর পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি ২
-
শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর
-
বিটিসিএল
-
জেলা তথ্য অফিস
-
পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড
-
জেলা শিক্ষা অফিস, যশোর
- স্থানীয় সরকার
- অন্যান্য প্রতিষ্ঠান
- ই-সেবা
- গ্যালারি
- যোগাযোগ
- অনাপত্তি সনদ ও ছুটি সংক্রান্ত
- আশ্রয়ণ প্রকল্প
- স্মার্ট বাংলাদেশ
-
-
প্রথম পাতা
-
-
জেলা সম্পর্কিত
জেলা পরিচিতি
ইতিহাস-ঐতিহ্য
ভৌগলিক ও অর্থনৈতিক
অন্যান্য
যশোর জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের ত্রান শাখার বিভিন্ন পত্র
ঐশ্বর্য ঐতিহ্যের যশোর (যশোরের প্রশাসনিক ইতিহাস)
- স্বাধীন রাজা প্রতাপাদিত্য
- যশোরের রাজাদের ইতিহাস, বিশেষত চাঁচড়া রাজার পারিবারিক ইতিহাস,
- বিখ্যাত জমিদারগণ ও জমিদারি প্রশাসন
- জেলার ভূ-সম্পত্তির বিভাজন এবং নতুন জমিদারের ইতিহাস
- ১৭৮১ সালে যশোর জেলায় বৃটিশ প্রশাসনের প্রতিষ্ঠা
- প্রথম ম্যাজিস্ট্রেট ও জাজ জনাব টিলম্যান হেঙ্কেল এবং তার সহকারী জনাব রকি
- ১৭৮৬ সালে যশোর কালেক্টরেট প্রতিষ্ঠার ইতিহাস
- যশোর কালেক্টরের দায়িত্ব ও কর্তব্য
- ভূমি রাজস্ব প্রশাসনের ইতিহাস
- অন্যান্য খাতভিত্তিক রাজস্ব প্রশাসন
- প্রাথমিক পুলিশ প্রশাসন (১৭৮১-৯০) ও অপরাধচিত্র
- অপরাধ বিচারিক প্রশাসন (১৭৮১-৯০)
- দেওয়ানী বিচার প্রশাসন (১৭৮১-৯০)
- দেওয়ানী মামলার বিচারকের ক্ষমতা বৃদ্ধি
-
জেলা প্রশাসন
জেলা প্রশাসকের কার্যালয়
উপপরিচালক/অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক
কর্মকর্তা ও কর্মচারী বৃন্দ
শাখা সম্পর্কিত
সভার কার্যবিবরণী
গুরুত্বপূর্ণ তথ্য
ইনোভেশন কার্যক্রম
-
সরকারি অফিস
আইন-শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা বিষয়ক
শিক্ষা ও সংস্কৃতি
- জেলা শিক্ষা অফিস, যশোর
- জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস
- জেলা শিল্পকলা একাডেমী
- বাংলাদেশ শিশু একাডেমী
- যশোর পিটিআই,যশোর
- জেলা উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো, যশোর
- যশোর পলিটেকনিক ইন্সটিটিঊট,যশোর
- সরকারি টিচার্স ট্রেনিং কলেজ
- জেলা সরকারি গণগ্রন্থাগার, যশোর
- কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, যশোর
- টেক্সটাইল ভোকেশনাল ইন্সটিটিউট, যশোর।
মানব সম্পদ উন্নয়ন বিষয়ক
- বিসিক জেলা কার্যালয়, যশোর
- জেলা সমাজসেবা কার্যালয়
- শহর সমাজসেবা কার্যালয়, যশোর
- হাসপাতাল সমাজসেবা কার্যালয়, যশোর
- প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্র, যশোর
- প্রবেশন অফিসারের কার্যালয়, যশোর
- সরকারি শিশু পরিবার বালিকা, যশোর
- যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, যশোর
- মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর,যশোর।
- বিআরডিবি
- জেলা সমবায় কর্মকর্তার কার্যালয়, যশোর।
- জেলা কর্মসংস্থান ও জনশক্তি অফিস,যশোর
- ইসলামিক ফাউন্ডেশন
- জেলা ক্রীড়া অফিসারের কার্যালয়,যশোর
- জাতীয় মহিলা সংস্থা, জেলা অফিস, যশোর
কৃষি, মৎস্য, প্রাণি ও খাদ্য বিষয়ক
- কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, যশোর
- জেলা মৎস্য অফিসারের কার্যালয়, যশোর
- বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (সার) যশোর অঞ্চল , যশোর
- জেলা প্রাণিসম্পদ অফিস
- জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়, যশোর
- আঞ্চলিক কৃষি গবেষণা কেন্দ্র, যশোর
- জেলা কৃত্রিম প্রজনন কেন্দ্র, যশোর
- সরকারী হাঁস মুরগি খামার, যশোর
- আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কর্মকর্তার কার্যালয়, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, যশোর।
- বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বীজ), যশোর
- তুলা উন্নয়ন বোর্ড,যশোর
- কৃষি বিপণন অধিদপ্তর
- পাট অধিদপ্তর,যশোর
- জেলা বীজ প্রত্যয়ন অফিসারের কার্যালয়,যশোর
- মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইন্সটিটিউট(এস আর ডি আই), যশোর
- তত্ত্ববধায়ক প্রকৌশলী কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন
- বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ, যশোর
- মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট, আঞ্চলিক গবেষণাগার, যশোর
- আঞ্চলিক প্রাণিরোগ অনুসন্ধান গবেষণাগার (এফডিআইএল), যশোর
স্বাস্থ্য ও পরিবেশ বিষয়ক
প্রকৌশল এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি
- তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর, যশোর
- কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর, যশোর
- নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয়, স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর(এইচইডি), যশোর বিভাগ
- জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন
- নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয়, স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর(এইচইডি), যশোর বিভাগ
- জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর
- গণপূর্ত বিভাগ
- নির্বাহী প্রকৌশলী (সওকা), বিএডিসি, যশোর রিজিয়ন, যশোর
- স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর
- সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর , যশোর
- পানি উন্নয়ন বোর্ড
- বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ-২, ওজোপাডিকো, যশোর
- বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ-১, ওজোপাডিকো, যশোর
- যশোর পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-১
- যশোর পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি ২
- শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর
- বিটিসিএল
- জেলা তথ্য অফিস
- পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড
ভূমি ও রাজস্ব বিষয়ক
অন্যান্য অফিস
-
স্থানীয় সরকার
জেলা পরিষদ
পৌরসভা
উপজেলা পরিষদ
ইউনিয়ন পরিষদ
-
অন্যান্য প্রতিষ্ঠান
শিক্ষা প্রতিষ্ঠান
সংস্থা/সংগঠন
-
ই-সেবা
জেলা ই সেবা কেন্দ্র
জাতীয় ই সেবা
মোবাইল অ্যাপ
ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার
অন্যান্য সেবা
-
গ্যালারি
ফটোগ্যালারি
ভিডিও গ্যালারি
-
যোগাযোগ
যোগাযোগের ঠিকানা
-
অনাপত্তি সনদ ও ছুটি সংক্রান্ত
অর্ডার সমূহ
- আশ্রয়ণ প্রকল্প
-
স্মার্ট বাংলাদেশ
কার্যক্রমসমূহ
কোন জেলার শিল্প, ব্যবসা ও বাণিজ্যের উদ্ভব ও ক্রমবিকাশের ক্ষেত্রে সে জেলার ভৌগোলিক অবস্থান, কৃষি ও যোগাযোগ ব্যবস্থা বিশেষ বা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। বৃহত্তর যশোর জেলা বাংলাদেশের পশ্চিম সীমান্তে অবস্থিত গাঙ্গেয় বদ্বীপ অঞ্চলের একটি জেলা। বঙ্গোপসাগর এ জেলা থেকে প্রায় ৭০/৭৫ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত। ঢাকা এবং অন্যান্য জেলার গুরুত্বপূর্ণ নগর বন্দরগুলির সঙ্গে বাস, লঞ্চ, রেল ইত্যাদির মাধ্যমে এ জেলার যোগাযোগ রয়েছে। এছাড়া যশোর ও ঢাকার মধ্যে নিয়মিত বিমান চলাচলের ব্যবস্থা আছে। সামুদ্রিক বন্দর চালনা যশোর সদর থেকে ৫৫/৬০ মাইল দূরে অবস্থিত। এ জেলার ভূমি তুলনামুলকভাবে কিছুটা উচু এবং শুস্ক। অধিকাংশ অঞ্চল বন্যায় প্লাবিত হয় না। জেলার সর্বত্রই প্রচুর খেঁজুর গাছ দেখা যায়। অন্যান্য ফসলাদির মধ্যে ইক্ষু, মরিচ, ধান, কলাই, মসুর, ছোলা,আদা,পান, তামাক প্রভৃতি পর্যাপ্ত পরিমাণে জন্মে। এই অঞ্চলের অধিবাসীদের জীবনধারণের ক্ষেত্রে কৃষিই প্রধান পেশা। এখানে শিল্পের কোন ভূমিকা তেমন নেই বললেই চলে। জেলার জনসংখ্যার প্রায় শতকরা ১৪ ভাগ লোক শিল্পের সাথে জড়িত। ১৯৬২ সালের শেষ দিকে জেলায় কুটির শিল্পের সংখ্যা ছিল ২৯,৬৪৬ এবং ক্ষুদ্র লিল্পের সংখ্যা ছিল ৫১৫ টি। কুটির ও ক্ষুদ্র এই দুই প্রকার শিল্পে যথাক্রমে ৮৮,৭৩০ এবং ৩,৪১৬ জন লোক নিয়োজিত ছিল। বর্তমানে চালু শিল্পগুলির মধ্যে কুটির শিল্পই প্রধান্য লাভ করেছে। যার ফলে মোট শিল্প শ্রমিকের শতকরা ৯০ ভাগেরও বেশী এই কুটির শিল্পে নিয়োজত আছে। জেলার কুটির শিল্পের মধ্যে খেজুরের গুড় শিল্প সর্বাপেক্ষা বেশী প্রসিদ্ধ। বৃটিশ শাসনের সময়েও যশোর খেজুর গুড়ের জন্য পরিচিত ছিল। ১৯৬০ সাল পর্যন্ত জেলায় কোন বৃহৎ শিল্প ছিল না। বর্তমানে যে কয়টি বৃহৎ শিল্প এখানে গড়ে উঠেছে সেগুলো হচ্ছে যশোর জুট ইন্ডাষ্ট্রীজ লিমিটেড, কার্পেটিং জুট মিলস্ এবং বেঙ্গল টেক্সাটাইল মিলস্ লিমিটেড। সবকটি শিল্প প্রতিষ্ঠানই অভয়নগর থানাধীন নোয়াপাড়ায় অবস্থিত। জেলার অন্যান্য থানার চেয়ে শিল্পের দিক দিয়ে অভয়নগর থানা অনেক অগ্রসর।
প্রাচীন শিল্পসমূহঃ
চিনি: অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগ থেকেই যশোর খেজুরের গুড়ের জন্য প্রসিদ্ধ লাভ করেছিল। ১৭৯২ খ্রীষ্টাব্দের অফিস নথিপত্রে দেখঅ যায় যে, তখন খেজুরের গুড় যশোরে পর্যাপ্ত পরিমাণে উৎপন্ন হতো এবং জেলার বাইরেও পাঠানো হতো। ১৭৯১ খ্রীষ্টাব্দে তৎকালীন কালেক্টরের হিসাব অনুসারে যশোরে ২০,০০০ মণ গুড় উৎপাদন করা হয়েছিল এবং তার অর্ধেক কলকাতায় চালান দেওয়া হয়েছিল। অবশ্য এই বিশ হাজার মণ গুড়ের মধ্যে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ ছিল ইক্ষুর গুড়। পরবর্তীকালে খেজুরের গুড়ের বাজার চাহিদা অনেক বেড়ে গিয়েছিল। কতিপয় ইংরেজ যশোরের কোটচাঁদপুর, তাহেরপুর, চৌগাছা, কেশবপুর, ত্রিমোহিনী, ঝিকরগাছা প্রভৃতি খেজুর গাছ প্রধান এলাকায় খেজুর গুড়ের কারখানা স্থাপন করেন। ফলে উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় এ জেলা চিনি শিল্পে অগ্রগতি লাভ করে। পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান জেলার ধোবা নামক স্থানে মিঃ ব্ল্যাক একটি চিনির কারখানা স্থাপনের উদ্যেগ গ্রহণ করেন। ধোবা চিনি কোম্পানী এই জেলার কোটচাদপুর এবং ত্রিমোহিনীতে বিলেতী যন্ত্রপাতি এনে চিনির কারখানা স্থাপন করে। পরবর্তী পর্যায়ে কোটচাদাপুর কারখানাটি মিঃ নিউহাউসের হাতে আসে। মিঃ সেইন্টবারী ত্রিমোহিনী কারখানার ভার গ্রহণ করেন এবতং ৩/৪ বছর চালাবার পর কারখানাটি বন্ধ করে দেন। ১৮৪২ খ্রিষ্টাব্দে কলকাতার গ্লাড সেউন উইলি অ্যান্ড কোম্পানী চৌগাছায় একটি কারখানা স্থাপন করে। প্রথমে মিঃ স্মিথ ও পরে মিঃ ম্যাকপিওল্ড এ কারখানা পরিচালনা করেন। চৌগাছা এবং কোটচাদপুরের কারখানা দুটি ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দের পরেও অনিয়মিতভাবে চালু ছিল। ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে মিঃ নিউ হাউস তাহেরপুরে একটি কারখানা স্থাপন করেন। দুবছর চালু থাকার পর কারখানাটি বিক্রি করে দেওয়া হয় এবং এর পরে এটি আখের রস থেকে তৈরী মদের কারখানায় রূপান্তরিত করা হয়।
উপরোক্ত বিবরণ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, চিনি পরিশোধনের বৃটিশ কারখানাগুলির ইতিহাস মোটেও সাফল্যের নয় বরং ব্যর্থতার। এ সম্পর্কে মিঃ এল, এস, এস, ও ম্যালি তার ‘‘যশোর জেলা গেজেটিয়ার’’ এ লিখেছেন (১৯১২) বৃটিশদের দ্বারা চিনি শিল্প গড়ে উঠার পরই স্থানীয় ব্যবসায়ীরা এ শিল্পের ক্ষেত্রে এগিয়ে আসে। বাজারে স্থানীয় ব্যবসায়ীদের দ্বারা পরিশোধিত চিনির চাহিদা বৃটিশদের কারখানায় উৎপাদিত উৎকৃষ্ট মানের চিনির চেয়েও বেশী থাকায় বৃটিশরা চিনির ব্যবসা হারায়। স্থানীয় ব্যবসায়ীদের মধ্যে যারা এ ব্যবস্থার সূত্রপাত করেন তারা ছিলেন ‘ময়রা’ সমপ্রদায়ের লোক। মিষ্টান্ন প্রস্তুতকারক সমপ্রদায়কে ম্যায়রা (গধুৎধ) বলা হতে। প্রায় ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দ থেকে তারা এ ব্যবসা শুরু করেন। এ ব্যাপারে বিখ্যাত ব্যবসায়ী হিসাবে নদীয়া জেলার দৌলতগঞ্জ এলাকার রাম সেন, বর্ধমান জেলার সাতগাছিয়া এলাকার ভগবান দে এবং নদীয়া জেলার শান্তিপুর এলাকার দশরথ ইন্দ্রের নাম উল্লেখ করা যায়। এরা কালক্রমে চিনি ব্যবসাকে তাদের একচেটিয়া ব্যবসায় পরিণত করে এবং ১৯৮০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত এ ব্যবসা পুরোদমে চালু রাখে। এরপরে বিদেশ থেকে আমদানীকৃত চিনির সংগে প্রতিযোগিতায় তাদের ব্যবসায় মন্দাভাব দেখা দেয়।
বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে যে সমস্ত শোধনাগার চালু ছিল সেগুলি সবই ছিল সেকেলে ধরনের। ফলে এগুলির সংখ্যা ক্রমশঃ হ্রাস পেতে থাকে। ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে যে সংখ্যা ১১৭ ছিল তা ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দে ৫০টিতে নেমে আসে। আমদানীকৃত চিনির সাথে স্থানীয় শোধিত চিনি প্রতিযেগিতায় টিকতেনা পারাটাই ছিল দেশীয় শোধনাগারগুলির বিলুপ্তির প্রধান কারণ। বঙ্গীয় কৃষি বিভাগের ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে প্রকাশিত ত্রৈমাসিক পত্রিকায় খেজুর গুড় বিষয়ক প্রবন্ধের উল্লেখ করে মিঃ ও’ম্যালী তার যশোর গেজেটীয়ারে দেখিয়েছেন যে, সমগ্র অবিভক্ত বাংলায় ১৫,৫৯, ৬৭৯ মণ খেজুরের গুড়ের মধ্যে যশোরে উৎপন্ন হত সেই সংখ্যাকে অত্যন্ত অতিরঞ্জিত বলে অভিহিত করেন। তার মতে এই শোধনাগারগুলোর উৎপাদন ক্ষমতা কেবল মাত্র ১,৮০,০০০ মণ এবং কেশবপুর এলাকার কৃষকদের তৈরী চিনির পরিমাণ উল্লিখিত সংক্যায় এক পঞ্চমাংশ। সমগ্র জেলায় বাৎসরিক চিনির উৎপাদন আড়াই লক্ষ মণের বেশী হতে পারে না। কারণ প্রকৃত হিসাব মতে ৬০ লক্ষ খেজুর গাছ থেকে খুব বেশীহলে ২৫ লক্ষ মণ গুড় উৎপাদিত হতে পারে। এই পরিমাণ গুড়কে পুরঃশোধন করলে খুব বেশী হলে ১০ লক্ষ মণ চিনি হতে পারে। সুতরাং উক্ত পত্রিকায় প্রকাশিত চিনির পরিমাণ নিঃসন্দেহে অতিরঞ্জিত। প্রকৃত পক্ষে কেবল মাত্র এক চতুর্থাংশ অথবা এক পঞ্চমাংশ গুড়কে পুন:শোধন করে চিনিতে পরিণত করা হত এবং অবশিষ্টাংশ স্থানীয়ভাবে ব্যবহৃত হতো। এছাড়া কিছু গুড় (কাঁচা অবস্থায় অথবা চিটাগুড় হিসাবে) পূর্ব বাংলায় চালান দেওয়া হতো। কাজেই খুব বেশী করে হিসাব ধরা হলেও পুনঃশোধনকৃত চিনির পরিমাণ ৩ লক্ষ মণের বেশী হতে পারে না।’’ যশোর জেলায় ইক্ষু থেকেও চিনি প্রস্তুত করা হতো। কিন্তু ইক্ষুর রস থেকে চিনি তৈরী ব্যয়বহুল বিধায় বেশী পরিমাণে উৎপাদন করা হতো না।
নীল: যশোরের প্রাচীন এবং বিলুপ্ত শিল্পসমূহের মধ্যে নীল শিল্পের নাম উল্লেখযোগ্য। এই শিল্প ১৮৯৫-৯৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত জেলার অর্থনৈতিক উন্নয়নে এক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে। ১৭৯৫ খ্রীষ্টাব্দে যশোর জেলায় ইউরোপীয়রা নীল চাষের সূত্রপাত করে। ১৭৯৫ খ্রীষ্টাব্দে জনৈক মিঃ বন্ড রূপদিয়ায় সর্বপ্রথম নীলের কারখানা স্থাপন করেন। জেলার নীল চষের আদি প্রবর্তক হিসাবে মেসার্স টাফট, টেইলার এবং ডঃ অ্যান্ড্রজ-এর নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দ নাগাদ যশোর (বর্তমান জেলা সদর এলাকা) নীল চষের একটি উল্লেখযোগ্য কেন্দ্রে পরিণত হয়। কিন্তু নীল শিল্পের সবচেয়ে বড় কারখানাগুলো গড়ে উঠে বর্তমান মাগুরা এবং ঝিনাইদহ জেলায়।
নীল উৎপাদনের জন্য নীলকরগণ ব্যাপকভঅবে জমি দখল করে এবং প্রজা চাষীগণকে চুক্তিতে নির্দিষ্ট দরে (মজুরীর হার) নীল চাষ করতে বাধ্য করে। এই চুক্তির হার গোড়ার দিকে ন্যায়সঙ্গত ছিল। শ্রমের মূল্য ক্রমশঃ বেড়ে যাওয়ায়বিশেষভাবে ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে বেল লাইন চালু হওয়ার পর থেকে কৃষকদের কাছে সেই হার খুব কম বলে মনে হয়। কিন্তু নীলকরগণ তাদের পূর্বের চুক্তি মোতাবেকই কৃষকদের পাওনা পরিশোধ করার জিদ ধরে থাকে। সেই সময় অন্যান্য ফসলের মূল্য তুলনামুলকভাবে বেড়ে যাওয়ায় কৃষকদের কাছে নীল চাষের চেয়ে তৈল বীজ ও খাদ্য শস্যের চাষ বেশী লাভজনক ছিল।
অবাধ্য প্রজাদের নিয়ন্ত্রণ আনতে গিয়েও খাজনা আদায়ের ব্যাপারে বেশ সমস্যা দেখা দেয় এবং ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে নীল চাষ ও খাজনা আদায় জনিত গোলযোগ নিষ্পত্তি করার জন্য সরকারকে অবশেষে একটি বিশেষ কমিশন গঠন করতে হয়। সরকারের সব রকামের সাবধানতা সত্বেও বিভিন্ন জায়গায় ভয়াবহ দাঙ্গা-হাঙ্গামার ফলে বেশ কিছু সংখ্যক জীবনহানি হয়। অতঃপর এসব বিশৃঙ্খলা দূর করার জন্য কিছু প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। পরিস্থিতির কিছু উন্নতি হলেও নীল চাষ মারাত্মকভঅবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এরপর নীল শিল্পের আর কোন উন্নতি হয়নি বরং ধীরে ধীরে বিলুপ্তির পথে এগিয়ে যায়।
কর্ণেল জে, ই, গ্যাসট্রেল তার রাজস্ব জরিপ রিপোর্টে উল্লেখ করেন যে, ১৮৬৮-৬৯ খ্রীষ্টাব্দে যশোরে দুই লক্ষ বিঘা জমি নীল চাষের আওতায় ছিল। কিন্তু কার্ণেল গ্যাসট্রেল কর্তৃক প্রতিবেদন পেশের চার বৎসর পর মিঃ রাম শংকর সেনের লিখিত বিবরণে দেখা যায় যে, সে সময় যশোরে নীল চাষের অধীনে জমির পরিমাণ ছিল প্রায় একলক্ষ বিঘা। রাম শংকর প্রজাদের সংগ বঙ্গবিরোধিতাকেই নীল চাষ হ্রাস পাওয়ার কারণ বলে মনে করেন।
১৮৯৫-৯৬ খ্রীষ্টাব্দে দেখা যায় যে, জেলায় ১৭টি নীলের কারখানা চালু ছিল। তন্মধ্যে নামকরা কারখানাগুলো ছিল হাজারহাটি, মদনধারী, জোড়াদহ, এবং পোড়াহাটি নামক স্থানে। এই কারখানাগুলি থেকে ১,৪১৬ মণ নীল উৎপন্ন হত এবং এর মূল্য ছিল সাড়ে তিন লক্ষ টাকা। চাষাবাদসহ নীল শিল্পের রক্ষণাবেক্ষণের ভার সম্পূর্ণভাবে ইউরোপীয়ানদের হাতে থাকায় স্থানীয় লোকেরা আর্থিকভাবে বিশেষ উপকৃত হত না। নীলের দাম শতকরা পঞ্চাশ ভাগ বৃদ্ধি পাওয়ায় এবং ইউরোপে এর বিকল্প উদ্ভাবিত হওয়ার ফলে এ দেশে নীলের চাষ সম্পূর্ণ লোপ পেয়ে যায়। হাজারাপুর, পোড়াহাটি, মদনধারী, বিজলী, চাউলিয়া, জোড়াদাহ, বাবুপুর এবং জেলার অন্যান্য জায়গায় ধ্বংসপ্রাপ্ত নীলকুঠিগুলি অতীতের নীল চাষের স্মৃতি বহন করছে।
বর্তমান শিল্পসমূহ চিরুনীঃ যশোর নামের সংগে জড়িয়ে আছে চিরুণীর ঐতিহ্য। এক সময় এই চিরুণীর সাড়া জাগানো সুনাম ছিল অখন্ড ভারত উপমহাদেশ জুড়ে। সে সুনাম ছড়িয়ে পড়েছিল শ্রীলংকা ও মিশরসহ সমগ্র আরবদেশে। বলতে গেলে উপমহাদেশের বাজার তখন ঝুকে পড়েছিল যশোরের দিকে। যশোরের ক্ষুদ্র শিল্পোগুলোর মধ্যে যশোর কোমব এন্ড নভেলটি ওয়ার্কস নামক চিরুণী কারখানাটি অন্যতম। এই শিল্প কারখানা ১৯৫৮ সালে এ শহরের শেখখালী এলাকায় স্থাপিত হয়। প্রথমাবস্থায় ৮ জন শ্রমিক নিয়ে এর কাজ শুরু হয়। এখানকার দ্রব্যাদির মধ্যে চিরুণী, স্যুটকেস ও পাউডার কেস উল্লেখযোগ্য। এছাড়া ১৯৭৭ সালের ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প সংস্থার জরিপে দেখঅ যায় যে, যশোরে বোতাম ও চিরুণী তৈরির কারখানা রয়েছে তিনটি।
প্রতিষ্টালগ্ন থেকে যশোরের চিরুণীর সুনাম আস্তে আস্তে সর্বত্র ছড়িয়ে পড়তে থাকে।
১৯৫৮ সাল পর্যন্ত যশোরের চিরুনী শিল্পের পথ পরিক্রমা ছিল মোটামুটি কন্টকমুক্ত। এ সময় পর্যন্ত চিরুনী তৈরির কাঁচামাল সেলুলয়েডের উপর আমদানী করা ছিল না। ১৯৫৯ সালে প্রথম এর উপর কর আরোপিত হয়। সেই সময় শুরু হয় চিরুণী শিল্পর দুর্দশার ইতিহাস।
যশোরের চিরুণী শিল্পের বিপর্যয়ের অন্যমত কারণ হচ্ছে আন্তর্জাতিক বাজারে সেলুলয়েডের মূল্য বৃদ্ধি। এর উপরে রয়েছে উৎপাদনের খরচ, ব্যাংকের সুদ, বিক্রয় কর, আমদানী কর, আবগারী শুল্ক প্রভৃতির ধাক্কা। যশোরের চিরুণীর তুলনায় ভারতীয় চিরুণীর দাম প্রায় অর্ধেক। খুব সহজেই বিপুল পরিমাণ ভারতীয় চিরুণী চোরাচালান হয়ে যশোরে চলে আসে এবং বাংলাদেশের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে।
বলা হয়ে থাকে যশোরের হাড়ের চিরুনীর প্রথিবী খ্যাত। প্রকৃতপক্ষে হাড়ের চিরুণী যশোরে কোন দিনও তৈরি হতো না। এখনও হয় না। ১৯৬৪ সাল পর্যন্ত মোষের শিং থেকে চমৎকার চিরুণী তৈরী হতো। ১৯৬৫ সালের পাক-ভারত যুদ্ধের পর ভারত থেকে মোষের শিং আমদানী বন্ধ হয়ে যায়। তখন থেকে শুধু সেলুলয়েডের চিরুনীই তৈরী হয়ে আসছে। আমাদের দেশের মোষের শিং উন্নতমানের নয়। এ থেকে মানসম্পন্ন চিরুনী তৈরী হয় না বলে তৈরিতে ভাটা পড়েছে।
সময়ের আবর্তে যশোরের চিরুনী শিল্প আজ এমন এক পর্যায়ে গড়িয়েছে যেখান থেকে সরকারী আনুকুল্য ছাড়া টিকে থাকার মতো অবস্থা আর নেই। এই শিল্পের উন্নয়নে সরকারী সহায়তা পেলে এ শিল্প দেশের চাহিদা মিটিয়েও পর্যাপ্ত পরিমাণে চিরুনী বিদেশে রপ্তানী করে বিপুল বৈদেশিক মুদ্রা আয় করতে একদিকে যেমন সমর্থ হবে অন্যদিকে এ হারানো ঐতিহ্যও ফিরে পাবে।
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস